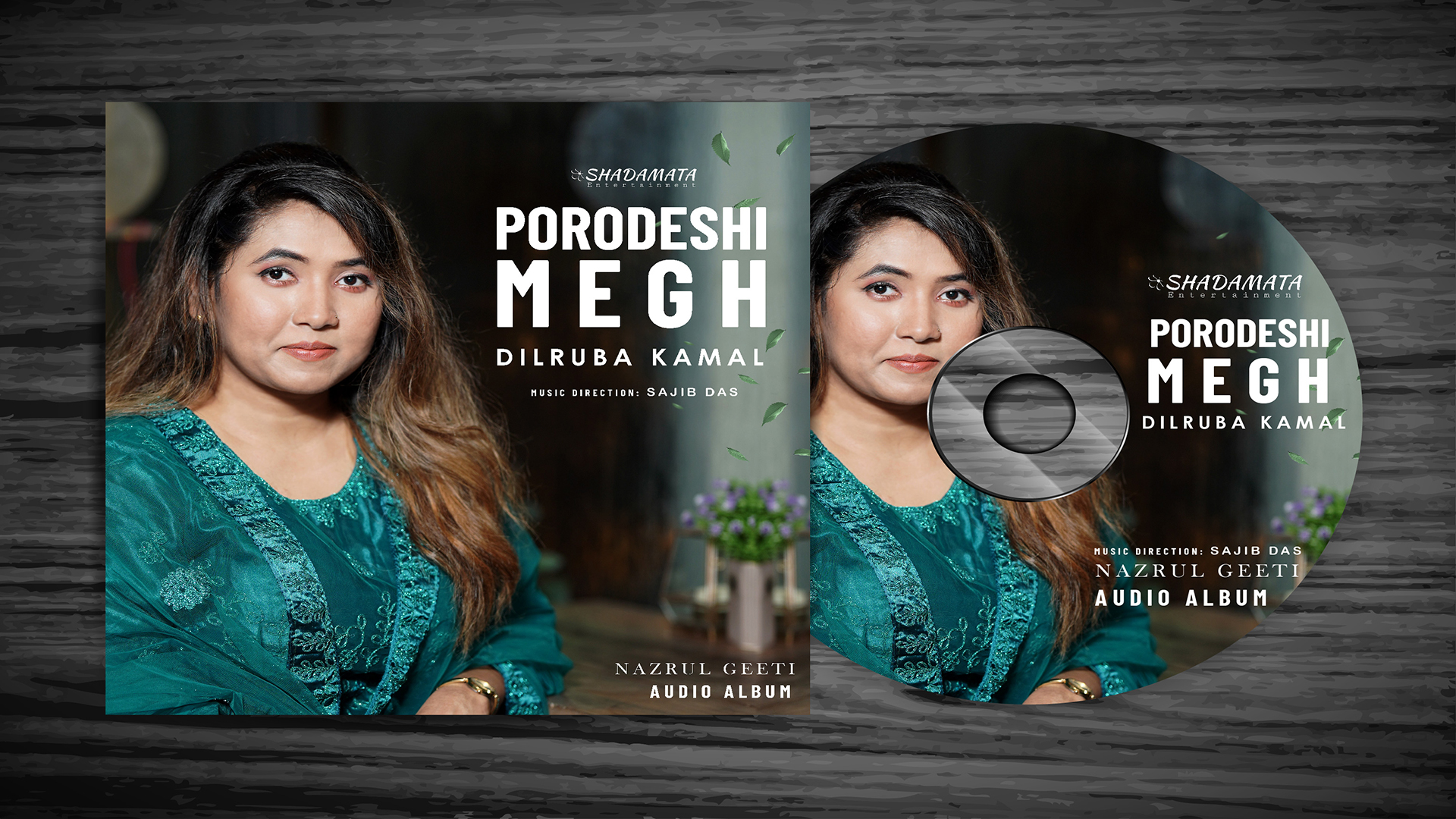গবেষক হতে চান? জেনে রাখুন এই ৫ প্রশ্নের উত্তর

- আপডেট সময় : ০৭:২৫:১৩ অপরাহ্ন, সোমবার, ৪ অগাস্ট ২০২৫
- / ১৮ বার পড়া হয়েছে
অনেকে মনে করেন—গবেষণা কেবলই উচ্চশিক্ষা বা বৃত্তির তহবিল পাওয়ার একটা সিঁড়ি। অবশ্য এটিও সত্যি, জাগতিক লাভকে পাশে রেখে একজন গায়ক যেমন গান ধরেন, কবি যেমন তাঁর ভেতরে চলতে থাকা ঝড়কে শব্দে রূপান্তর করেন, একজন গবেষকও মূলত নিজের মনের আনন্দেই গবেষণা করেন। গবেষণার প্রবল ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যাঁরা কেবল দিকনির্দেশনার অভাবে এগোতে পারছেন না।
প্রথম বর্ষ থেকেই কি গবেষণার কাজ শুরু করা সম্ভব?
বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার পরপরই একজন শিক্ষার্থীর জন্য গবেষণা শুরু করা একটু কঠিন। তা ছাড়া গবেষণা তো শুধু করলেই হয় না, এর জন্য বেশ শক্ত একটি ভিত তৈরি হওয়া লাগে। যদি এটাই না জানি—আমি কোন বিষয়ে গবেষণা করব, যে বিষয়টা নিয়ে ভাবছি সেই খাতে কী কী কাজ হয়েছে, নতুন কী করতে পারি যা কেউ করেনি; তাহলে গবেষণা শুরু করে লাভ নেই। এ কারণেই ‘আন্ডারগ্র্যাজুয়েট থিসিস’ করানো হয় চতুর্থ বর্ষে, প্রথম বর্ষে নয়। আমি নিজেই গবেষণা শুরু করেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় বর্ষে থাকাকালীন। তবে এমনও অনেককে দেখেছি, যারা প্রথম বর্ষ থেকেই গবেষণার কাজ শুরু করে তৃতীয় বর্ষের মধ্যে মূল লেখক (ফার্স্ট অথর) হিসেবে খুব ভালো জার্নালে গবেষণাপত্র প্রকাশ করে ফেলেছে। এমনও অনেকে আছে যারা কলেজ থেকেই ভালো কোনো ল্যাবে দল বেঁধে গবেষণার কাজ শুরু করে, ফলে ফার্স্ট অথর হতে না পারলেও দলগত কাজের অংশ হিসেবে ভালো ভালো গবেষণাপত্রে তাদের নাম থাকে।
গবেষণা কাদের জন্য, কাদের জন্য নয়?
সহজ করে বললে গবেষণা তাঁদের জন্য, যাঁরা শিক্ষক বা গবেষক হতে চান। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যেমন প্রতিবছর এক বা একাধিক গবেষণাপত্র প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থাকে (যদিও বাংলাদেশে এই চল নেই। বাইরের অনেক দেশেই কোনো শিক্ষক গবেষণাপত্র প্রকাশ না করে এক বছর বসে আছেন, এটা অকল্পনীয়)। যাঁরা বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিতে চান, তাঁদের জন্যও গবেষণাপত্র প্রকাশ বেশ দরকারি। কারণ, এর মাধ্যমে যে অধ্যাপকের অধীনে আপনি গবেষণা করতে যাবেন, তিনি আপনার কাজ ও আগ্রহের ক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা পাবেন। আমি এখন যে শিক্ষকের অধীনে পিএইচডি করছি, তিনি আমার মাস্টার্সের থিসিস দেখেই আমার কাজ পছন্দ করেছিলেন, যেটাকে আমি পরে গবেষণাপত্র আকারে প্রকাশ করি। মোটাদাগে বললে, আপনার যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিটা নিয়েই চাকরিতে ঢুকে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকে, তাহলে গবেষণায় তেমন সময় না দিলেও চলবে। তবে হ্যাঁ, সব ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম থাকতে পারে। যেমন কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান চাইতেই পারে যে তাদের নিজস্ব গবেষণার জন্য তাঁরা ভালো মানের গবেষণাপত্র আছে, এমন কাউকে নিয়োগ দেবে। এ ধরনের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা না করলেও গবেষণার অভিজ্ঞতা আপনাকে এগিয়ে রাখবে।
গবেষণা কীভাবে করব, কোন বিষয়ে করব?
অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই তৃতীয় বা চতুর্থ বর্ষে ওঠার পর গবেষণাপত্র লেখা শেখানো হয়। গবেষণাসংক্রান্ত আলাদা ক্লাস, সেমিনার বা কোর্স পাঠ্যক্রমে থাকে। তত দিনে শিক্ষার্থীরা তাঁদের ভালো লাগা বা আগ্রহের বিষয় সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যান। এর চেয়ে ছোট বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণার দিক ঠিক করা একটু কঠিন। অনেকেই যে বিষয়ে শুরু করেন, সেখান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয় নিয়ে পরে গবেষণা করেন। এমনও হয়, কেউ হয়তো স্নাতক করেছেন ‘স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে’, যেখানে তাঁর কাজ ছিল মূলত দালানকোঠা কীভাবে বানায় সে–সংক্রান্ত প্রকৌশলের ওপর, কিন্তু পরে তিনি পিএইচডি করেছেন ক্যানসার নিয়ে। অর্থাৎ পুরকৌশল থেকে একেবারে মেডিকেল সায়েন্স। যে কারও ক্ষেত্রেই এমন হতে পারে এবং এটা খুবই স্বাভাবিক।
বিষয় ঠিক হয়ে গেলে এ–সংক্রান্ত বড় বড় জার্নালের তালিকা করে ফেলতে হবে। গল্পের বইয়ের মতো প্রচুর গবেষণাপত্র পড়া শুরু করতে হবে। একজন গবেষক যত বেশি অন্য গবেষকের লেখা পড়েন, তত তাঁর জন্য ভালো মানের গবেষণা করা সহজ হয়। কারণ, গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন কাজ দেখাতে হয়। যে কাজ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে, তার তুলনায় আমার আইডিয়া বা কাজ কেন আলাদা, সেটা প্রমাণ করতে হয় লিটারেচার রিভিউ বা ইন্ট্রোডাকশন সেকশনে। গবেষণাপত্রের বিভিন্ন অংশ, কোন অংশে কোন বিষয় আলোচনা করতে হয়, কীভাবে দ্রুত ও কার্যকরভাবে বেশি গবেষণাপত্র পড়া ও লেখা যায়—এ নিয়ে ইউটিউবে অনেক ভিডিও পাবেন, চাইলে সেগুলো দেখে দেখেও জানাশোনা বাড়াতে পারেন। ফেসবুক বা লিংকডইনেও অভিজ্ঞজনেরা গবেষণা নিয়ে বিভিন্ন লেখা শেয়ার করেন। এগুলো সামনে এলেই পড়ে ফেলতে হবে। টানা এমন রুটিনে চললে গবেষণার ক্ষেত্রে দক্ষতা আপনাআপনিই বাড়তে থাকবে।
গবেষণাপত্র তো লিখলাম, কিন্তু এখন প্রকাশ করব কীভাবে?
গবেষণা মূলত তিনভাবে প্রকাশ করা যায়। এক—বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশ। যেকোনো জার্নাল বাছাই করলেই হবে না। ধরা যাক আমি কাজ করেছি বাংলাদেশের নদীর পাড় কেন ভাঙে এই বিষয়ে, কিন্তু লেখা জমা দিলাম সাংবাদিকতাবিষয়ক জার্নালে। এটা করলে তো তারা আমার লেখা প্রকাশ করবে না, এটাই স্বাভাবিক। কোন লেখা কোন জার্নালে দিলে প্রকাশ করার সম্ভাব্যতা বেশি, এটি বোঝা যায় সেই জার্নালের ‘এইম অ্যান্ড স্কোপ’ অংশটুকু পড়লে। প্রতিটি জার্নালই তাদের ওয়েবসাইটে বলে দেয় কোন ধরনের লেখা তারা সাধারণত প্রকাশ করে। সেটা পড়ে একজন গবেষককে বাছাই করতে হয়, জার্নালটি তাঁর লেখা প্রকাশের জন্য উপযুক্ত কি না।
দ্বিতীয় যে উপায়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ করা যায়, তার নাম কনফারেন্স পেপার। প্রতিদিনই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সম্মেলন পৃথিবীর কোথাও না কোথাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে গবেষকেরা নিজেদের কাজ উপস্থাপন করছেন। বাংলাদেশেও এমন সম্মেলন হয়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রতিবছর নিজেদের সম্মেলন আয়োজন করে। সেখানেও গবেষণাপত্র প্রকাশ করা যায়।
তৃতীয় পথ হলো থিসিস আকারে প্রকাশ। স্নাতক বা স্নাতকোত্তরের শেষ বর্ষে অনেক শিক্ষার্থীকেই এটা বাধ্যতামূলকভাবে করা লাগে।
গবেষণা কি আনন্দময় হতে পারে? নাকি গবেষণা মানেই ‘ক্লান্তিকর’ কাজ?
বিড়াল কি আমাদের মতো স্ট্র বা পাইপ দিয়ে দুধ খায়? না। বরং বিড়াল তার জিহ্বা এত দ্রুত ওঠানামা করায় যে দুধ খাওয়ার সময় পাত্র থেকে বিড়ালের গলা পর্যন্ত দুধের এক নল তৈরি হয়ে যায়, যেটা দিয়ে সহজে সে অনেক দুধ পান করতে পারে। এ গবেষণাটি যে গবেষক প্রকাশ করেছিলেন, তিনি কোনো জাত বিড়াল গবেষক নন, কাজ করতেন পানির গুণাগুণ নিয়ে। অবসর সময়ে বিড়াল আর বিড়ালের দুধ খাওয়া নিয়ে পড়ে থাকতেন। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বিড়ালের ছবি তুলতেন, ভিডিও ধারণ করতেন। একসময় তাঁর এই গবেষণা বিশ্ববিখ্যাত সায়েন্স জার্নালের কাভারে ছাপা হয়েছিল। আদতে গবেষণা করে যিনি আনন্দ পান, কাজটা যত ক্লান্তিকরই হোক না কেন, দিন শেষে সেই ‘ক্লান্তি’ তিনি গায়ে মাখবেন না। ৫০০ থেকে ১ হাজার বিড়ালের ছবি ও ভিডিও ধারণ করা আমার-আপনার কাছে অনেক কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু সেই গবেষকের জন্য এটা অনেক আনন্দের কাজ। আমি একবার স্কুলে পড়া এক শিক্ষার্থীকে দেখেছি, সে মশার কয়েলের বিকল্প খোঁজার চেষ্টা করছে। গ্রামে বসেই নানা গাছের পাতা পুড়িয়ে দেখছে, কোনোটা মশার কয়েলের চেয়ে ভালো কাজ করে কি না। হয়তো এই গবেষণা আজ থেকে কয়েক দশক আগেই কেউ করে ফেলেছে, কিন্তু তা–ও এটাই গবেষণার মূল আনন্দ। একটা কিছুর পেছনে বছরের পর বছর লেগে থেকে একটুখানি সফল হলেও মনটা যেভাবে প্রশান্তিতে ভরে যায়, তার সঙ্গে অন্য কিছুরই তুলনা হয় না।